 |
| প্রতীকী ছবি |
ধর্ম, রাজনীতি ও বুদ্ধিবৃত্তির বিভ্রম: ব্রিটিশ উত্তরাধিকার ও আজকের বাংলাদেশ
ধর্ম
ধর্ম আমাদের জন্য এক ধরনের ‘প্যারাসিটামল’— প্রতিটি সমস্যার নিবারণকারী ওষুধের মতো হয়ে গেছে। ব্রিটিশরা এই বিষয়টি খুব সূক্ষ্মভাবে উপলব্ধি করেছিল। ১৭৮০ সালে ফোর্ট উইলিয়ামের গভর্নর হেস্টিংস কলকাতায় আলিয়া মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করান। সেই থেকেই মাদ্রাসা শিক্ষা উপমহাদেশে বিস্তৃত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের প্রেক্ষাপটে মাদ্রাসাটি ঢাকায় স্থানান্তরিত হয়।
প্রতিষ্ঠার প্রথম দিকে মাদ্রাসার পরিচালনা ছিল ব্রিটিশ ও খৃষ্টান প্রশাসনের ওপর। ১৭৮১ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত এটি একটি বোর্ডের মাধ্যমে পরিচালিত হতো; সেক্রেটারি ছিলেন একজন খৃষ্টান এবং তাঁর সহকারী মুসলিম। ১৮৫০ সালে প্রিন্সিপাল পদের সৃষ্টির পর ১৯২৭ সাল পর্যন্ত মোট ২৬ জন প্রিন্সিপাল ছিলেন খৃষ্টান ধর্মাবলম্বী।
এখানে একটা প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে উত্থাপন করতে হয় — ব্রিটেনে আলিয়া মাদ্রাসা না গড়ে কেন কলকাতায় এটি প্রতিষ্ঠা করা হলো? মাদ্রাসা মূলত আরবি ও ইসলামি শিক্ষা–প্রতিষ্ঠান; তবু তার প্রধানের পদটি ‘প্রিন্সিপাল’ নামেই রাখা হলো। এটি ভাবতে বাধ্য করে — আমরা কি কোরআন-হাদিসের আলোকে স্বাধীনভাবে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি, নাকি বৌদ্ধিক নির্ভরতা এখনও বাইরের ব্যবস্থার ওপরই টিকে আছে? অনেক ক্ষেত্রেই ব্রিটিশদের প্রদত্ত নীতিমালা আমরা অমূল্য বিধান মনে করে গ্রহণ করে নিই।
উপমহাদেশের মানুষের মধ্যে ধর্মকে জীবনের এক অনুষঙ্গ হিসেবেই দেখা হয়েছে—হিন্দু হোক বা মুসলিম—অনেসব মানুষ ধর্মকে দৈনন্দিন আচরণের এক ‘অতিরিক্ত’ স্তর ভাবেন। ব্রিটিশ শাসকরা এই মনস্তত্ত্ব বুঝে উপযুক্ত কৌশল প্রয়োগ করে যে কোন জাতিকে যে ‘ট্যাবলেট’ খাওয়াতে হবে। সেই সময় জিন্নাহ পশ্চিমা সংস্কৃতির অনুরাগী ছিলেন; তিনি ধর্মীয় অনুশাসন কঠোরভাবে পালন করতেন না। গান্ধী ছিলেন গীতা-ভক্ত এবং উভয়ই লন্ডন থেকে বোধ ও রাজনীতিতে যুক্ত হন। জিন্নাহ ১৫ বছর ভারতের কংগ্রেসে জড়িত ছিলেন।
রাজনীতিতে সহজে সাফল্য ধরে নেওয়া যায় না—জিন্নাহর রাজনৈতিক উত্থানও অনেকটাই ঐতিহাসিক পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক সুযোগের ফল। ১৯৪০ সালে লাহোরে মুসলিম লীগের সম্মেলনে দ্বিজাতিতত্ত্বের ধারণা প্রকাশ পায়—এর পেছনে নানা ভুমিকা ও প্রসঙ্গ ছিল। ব্রিটিশেরা তাদের কৌশলে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল; পরে হিন্দু ও মুসলিম নিজেই আচরণ ও অবস্থান নিয়ে সংঘাতিত হয়। যতক্ষণ মানুষ মনে ‘ধর্ম’ নামক বিভাজন জাগিয়ে রাখবে, ততদিন বিভাজন ও সংঘাতের সম্ভাবনা রয়ে যাবে।
ঐতিহাসিকভাবে ওয়াজ-মাহফিলের প্রচলনও নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ফল। ১৯০৬ সালে ইব্রাহিম আলী তশনা নামক একজন বক্তা বৈঠক-আয়োজন শুরু করেন; এর আগ পর্যন্ত উপমহাদেশে ব্যাপকভাবে ওয়াজের প্রচলন ছিল না। ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে মাওলানা মোহাম্মদ কাশেম নানুতুবি দেওবন্দে কাওমী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন; এর প্রভাব পরে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে।
উৎপত্তিতে থাকা উদ্দেশ্য—ধর্ম প্রচার—আজ বহু ক্ষেত্রে রাজনৈতিক মঞ্চ কিংবা জনসমাগমের বিনোদনকেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। কিছু বক্তা এমন বিষয়ও আলোচনায় আনেন যা মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত। ফলে শ্রোতাদের মাঝে বিভ্রান্তি জন্মায় এবং ধর্মীয় বার্তা তার মৌলিকতায় বাসা বাঁধতে পারে না।
আজকের বাংলাদেশে শিক্ষা পদ্ধতি—আলিয়া, কওমী, সাধারণ বিদ্যালয়—এবং ধর্মীয় প্রথা সবকিছুকে একত্রে বিবেচনা করলে দেখা যায়, ধর্মীয় শিক্ষা অনেক সময় বাজারভিত্তিক একটি পেশায় পরিণত হয়েছে। সামাজিক অভ্যাস ও পোশাকচর্চায় ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থার প্রভাবও স্পষ্ট—কিছু আচরণ মনে হয় আমরা নিজেদের শিখিয়েছি, আবার কিছু সংস্কার বাইরের অনুকরণ। এর সঙ্গে কিছু গোষ্ঠী মানুষের মানসিকতায় প্রভাব বিস্তার করে, যা সমালোচনারও বিষয়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসমাজের মধ্যে নানা বুদ্ধিবৃত্তিক বিভ্রাট দেখা যায় — অনেকে আত্মবিশ্বাসী হলেও তত্ত্বগত দিশাহীনতা তাদের চিন্তার গভীরতাকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। অনেক সময় বইয়ের অনুবাদ থাকলেও তার অন্তর্নিহিত ভাব বা প্রাসঙ্গিকতা অনুধাবন করা হয় না; ফলে জনসমাজে একটি ‘শব্দজ্ঞানী’ প্রজন্ম তৈরি হচ্ছে, যারা স্রেফ দৃশ্যমান উদ্বোধনী বক্তব্যেই আত্মতুষ্টি পায়।
শেষ পর্যন্ত আমাদের প্রশ্ন হওয়া উচিত—ধর্মকে কি আমরা কেবলই প্রতিক্রিয়া বা তাত্ত্বিক স্বস্তি হিসেবে গ্রহণ করছি, নাকি তা সমগ্র সমাজকে গভীরভাবে শিক্ষিত ও নৈতিকভাবে গঠন করার উপায় হিসেবে ব্যবহার করছি? ধর্মের ভূমিকা যদি সমাজের যুক্তিবোধ ও মানবিক উন্নয়নে সীমাবদ্ধ না করে শুধুই আবেগপ্রসূত প্রতিক্রিয়ায় পরিণত হয়, তাহলে আমাদের মননের ক্ষত সার্বিক উন্নয়নকে আটকে দেবে।
মূল
লেখাঃ লুসিড ড্রিম(শুভ)
(সংশোধিত ও সম্পাদিত)

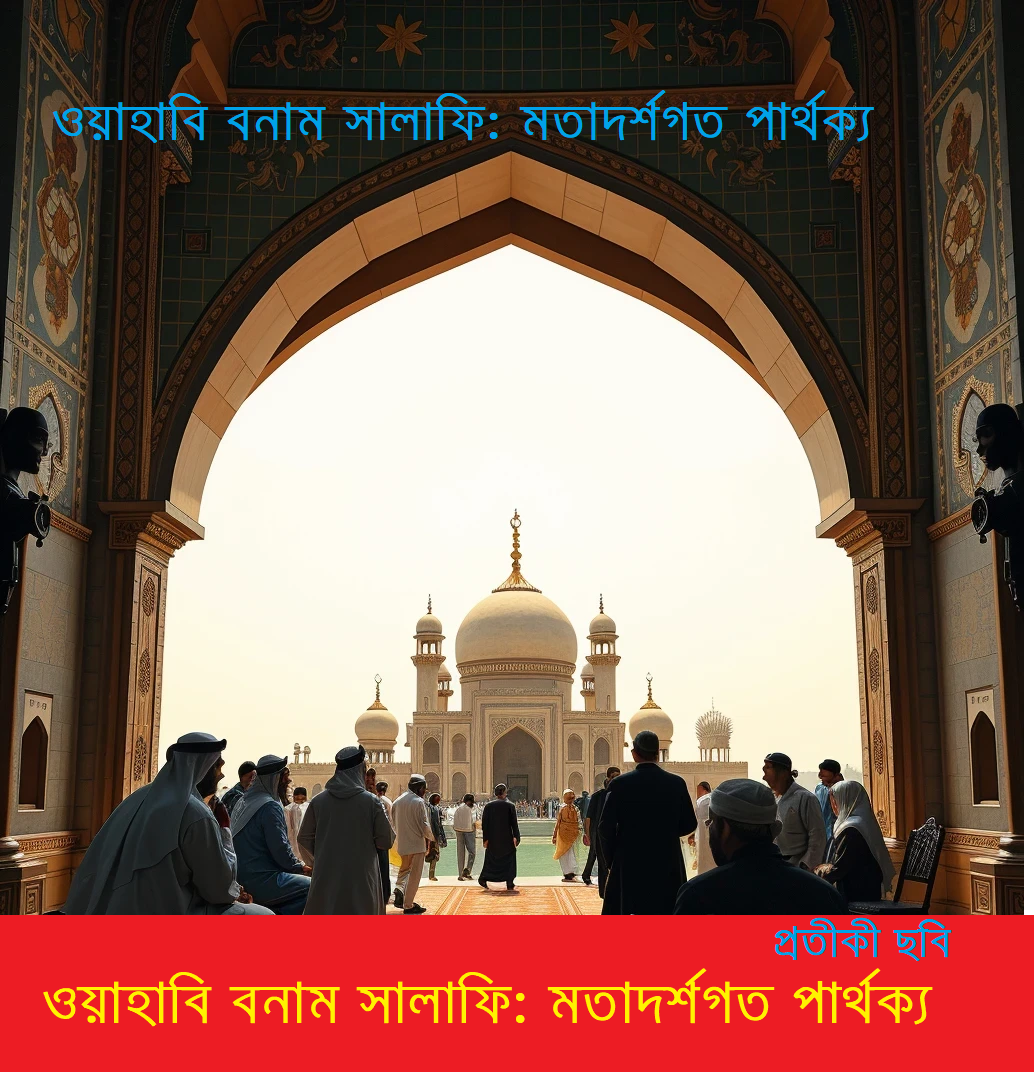

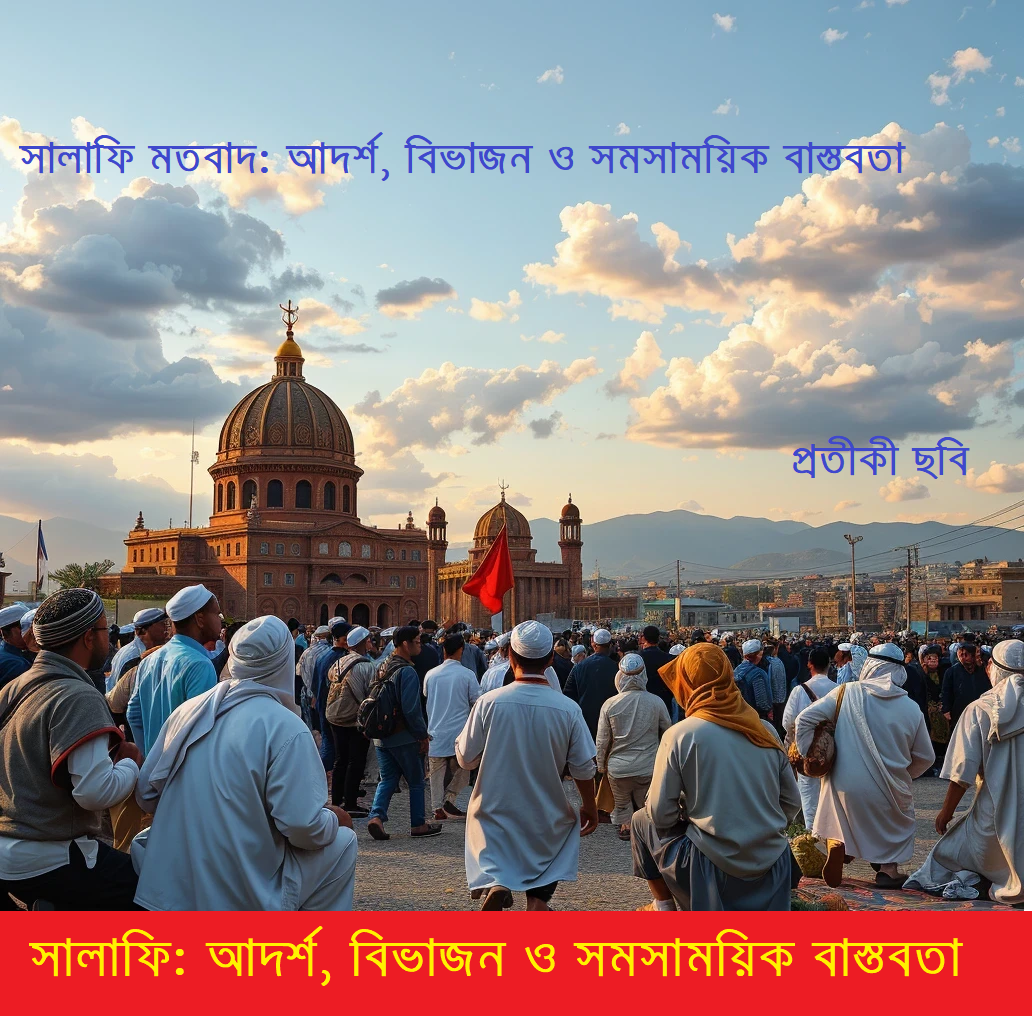

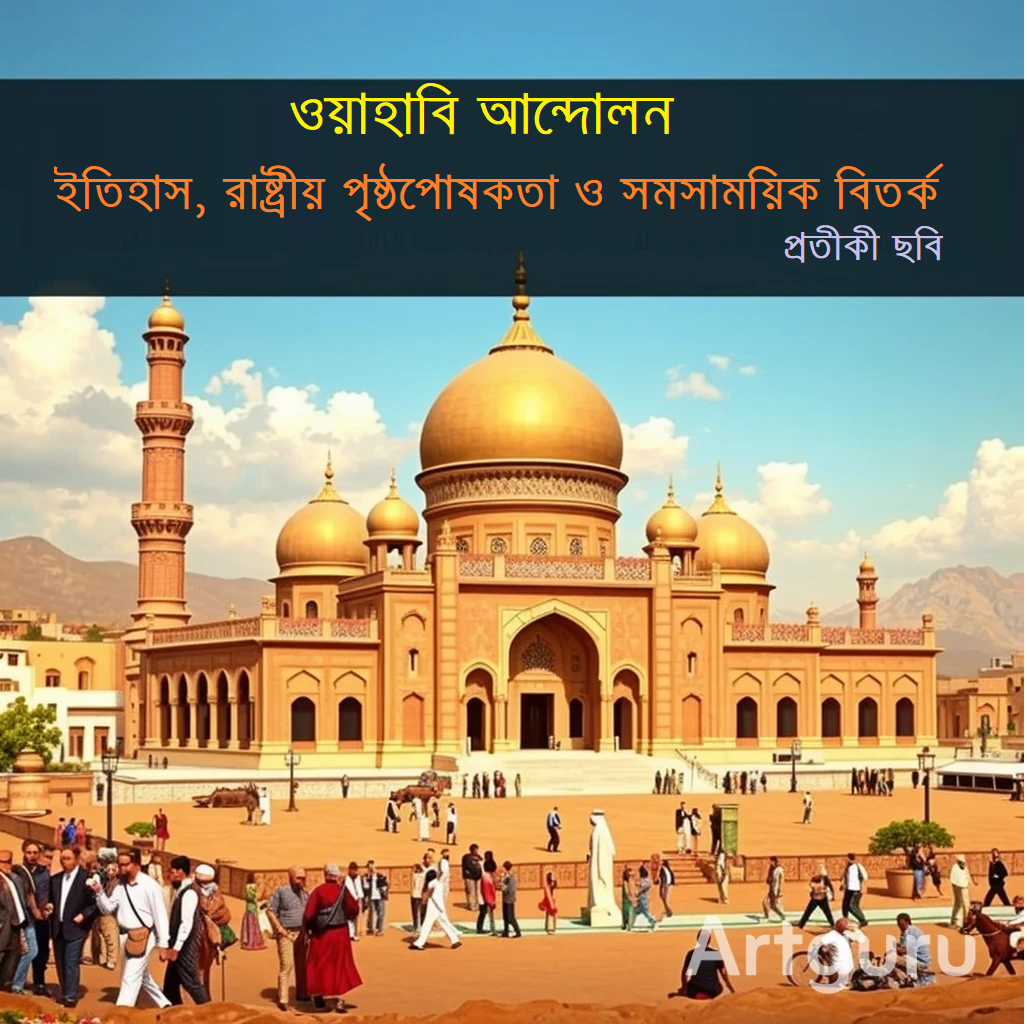

Leave a Reply